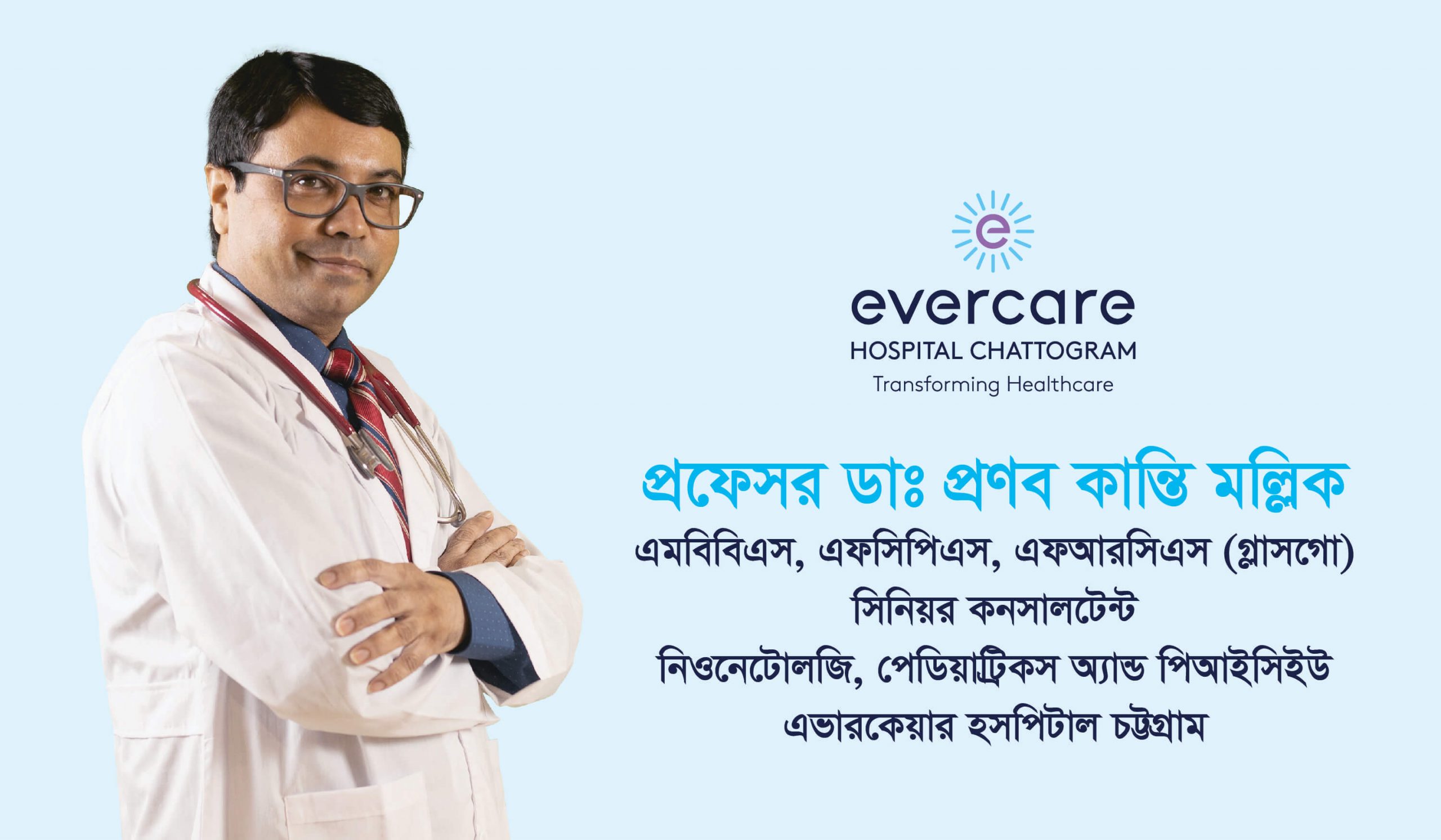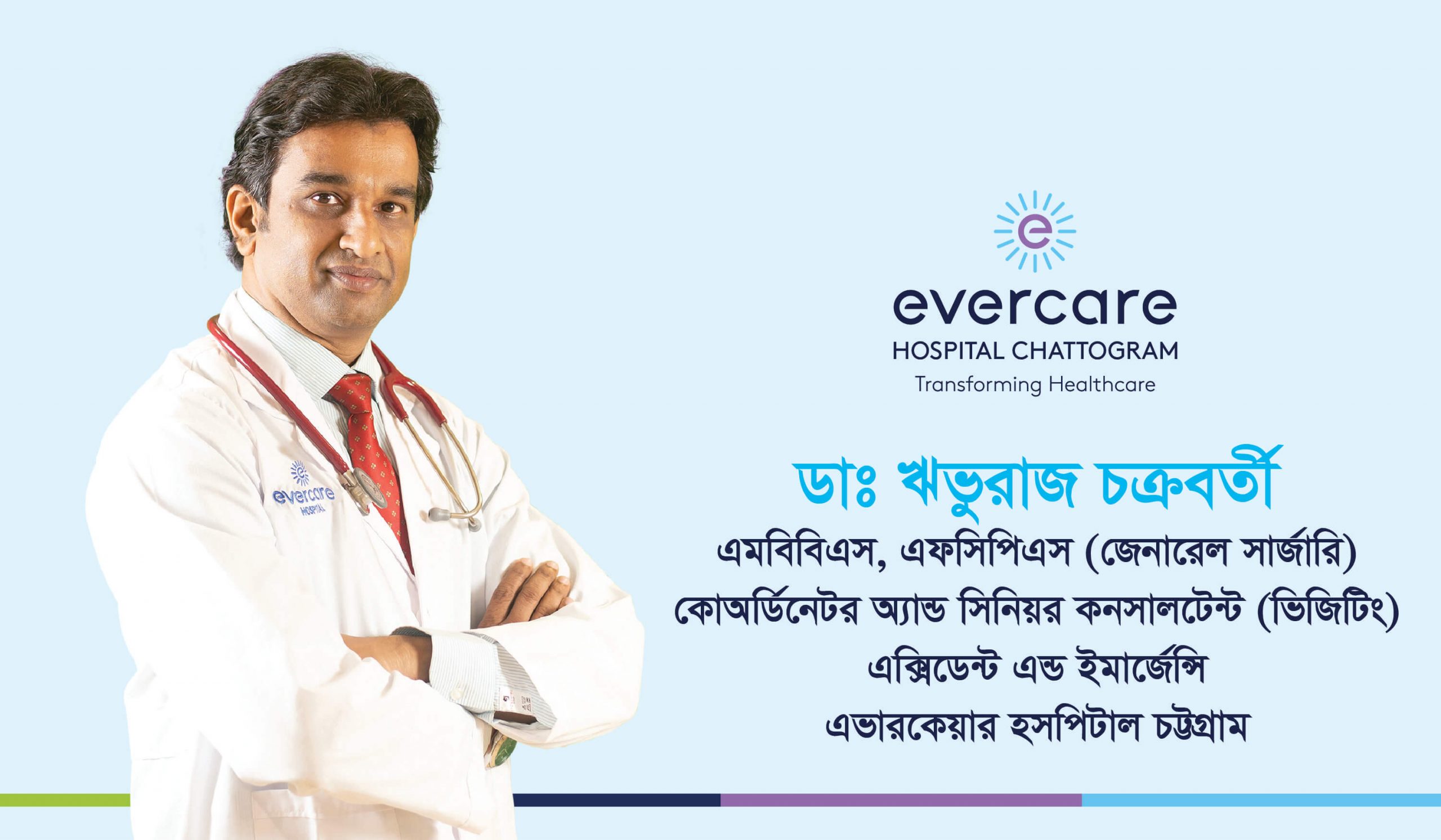কিডনি রোগ এবং গর্ভাবস্থা, দুটিই মহিলাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যখন এই দুটি একসাথে জড়িত হয়, তখন অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করা জরূরি। কিডনি রোগ থাকা অবস্থায় গর্ভধারণ করা, বা গর্ভাবস্থায় কিডনি রোগের জটিলতা দেখা দেওয়া, দুই ক্ষেত্রেই বিশেষ যত্ন প্রয়োজন।
কিডনি রোগ এবং গর্ভাবস্থা: কেন এত জটিল?
- গর্ভাবস্থায় শরীরের পরিবর্তন: গর্ভাবস্থায় একজন মহিলার শরীরে অনেক পরিবর্তন হয়। রক্তের পরিমাণ বাড়ে, কিডনিকে আরও বেশি কাজ করতে হয়। যদি এর আগে থেকেই কিডনি রোগ থাকে, তাহলে এই বাড়তি চাপ কিডনির উপর আরও পড়ে।
- গর্ভাবস্থা-জনিত কিডনি সমস্যা: কিছু ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থার কারণে নতুন কিডনি সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন, প্রেগন্যান্সি-ইন্ডুসড হাইপারটেনশন (গর্ভাবস্থা-জনিত উচ্চ রক্তচাপ) কিডনিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।
- ঔষধের সীমাবদ্ধতা: গর্ভাবস্থায় অনেক ওষুধ সেবন করা নিরাপদ হয় না। কিডনি রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত অনেক ওষুধই গর্ভবতী মহিলার জন্য নিরাপদ নয়।
কিডনি রোগ থাকা অবস্থায় গর্ভধারণ
যদি কোন মহিলার কিডনি রোগ থাকে এবং তিনি গর্ভধারণ করতে চান, তাহলে তাকে অবশ্যই একজন নেফ্রোলজিস্টের পরামর্শ নিতে হবে। নেফ্রোলজিস্ট হলেন কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি রোগীর কিডনির অবস্থা পরীক্ষা করে এবং গর্ভধারণের ঝুঁকি ও সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন।
গর্ভাবস্থায় কিডনি রোগের লক্ষণ
- সোজন: পা, হাত, মুখ ফুলে যাওয়া।
- উচ্চ রক্তচাপ: রক্তচাপের মাত্রা বেড়ে যাওয়া।
- প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া: প্রস্রাবের রং পরিবর্তন হওয়া।
- ক্লান্তি: সারাক্ষণ ক্লান্তি অনুভব করা।
- বমি বমি ভাব: বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
গর্ভাবস্থায় কিডনি রোগের চিকিৎসা
- ওষুধ: কিছু ক্ষেত্রে কিডনি রোগের চিকিৎসার জন্য নিরাপদ ওষুধ ব্যবহার করা হয়।
- ডায়ালাইসিস: যদি কিডনি পুরোপুরি কাজ না করে, তাহলে ডায়ালাইসিসের প্রয়োজন হতে পারে।
- গর্ভাবস্থার পরিচালনা: নিয়মিত চেকআপ, বিশ্রাম এবং সুষম খাদ্য গর্ভাবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সাহায্য করে।
কিডনি রোগ এবং গর্ভাবস্থা: সতর্কতা
- ডাক্তারের পরামর্শ: অবশ্যই একজন নেফ্রোলজিস্টের পরামর্শ নিন।
- নিয়মিত চেকআপ: গর্ভাবস্থার সময় নিয়মিত চেকআপ করান।
- ওষুধ সেবন: ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোন ওষুধ খাবেন না।
- সুষম খাদ্য: সুষম খাদ্য গ্রহণ করুন।
- বিশ্রাম: পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন।
কিডনি রোগ থাকা অবস্থায় গর্ভধারণ একটি জটিল বিষয়। তবে, সঠিক চিকিৎসা এবং যত্নের মাধ্যমে সুস্থ শিশু জন্ম দেওয়া সম্ভব।